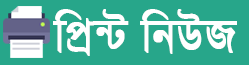
গত দুই দশকে বেড়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন। গেলো বছর একদিনে সর্বোচ্চ রেকর্ড ১৬ হাজার ৪৭৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের খবর জানিয়েছিল বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)। আর এই উৎপাদনের প্রায় পুরোটাই আসছে জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে।
অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বিদ্যুৎ খাতে সফলতার গল্প বলা হলেও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি বাংলাদেশ। যদিও ২০২০ সালের মধ্যেই মোট জ্বালানির ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য খাত থেকে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার।
এছাড়া, প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে ৬ দশমিক ৭-৩ শতাংশ থেকে ২১ দশমিক ৮-৫ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্য বাংলাদেশের। এজন্য ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার।
এ অবস্থায় আমদানি নির্ভর জ্বালানির ব্যবহার কমানো সবচেয়ে জরুবি। দেশের প্রয়োজনীয় জ্বালানি চাহিদা মেটাতে এই খাতকে নবায়নযোগ্য খাতে রূপান্তর করাও অপরিহার্য।
তবে, গেলো বছরগুলোর কর্মতৎপরতা আশাবাদী হওয়ার মতো নয়। প্রশ্ন হলো এ খাতে কেনো ব্যর্থ হলো দেশ? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সদিচ্ছা না থাকায় এই খাতে অগ্রগতি হয়নি।
কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্বালানি উপদেষ্টা অধ্যাপক এম শামসুল আলম বলেন, আমরা সোলার সিস্টেমে মডেল হয়ে গেলাম বিশ্বে, চোখের সামনে দেখলাম সেই সোলার সিস্টেম অপ্রচলিত হয়ে গেলো। মানুষ প্রত্যাখ্যান করলো কিন্তু সোলার সিস্টেম দিয়ে আসলেই আমাদের দেশের তৃণমূল মানুষের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো যেত এবং তাদের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেত। যদি প্রযুক্তিগতভাবে যথাযথ এর মান উন্নয়ন করতাম।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশে এখনও নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়নি। অর্থব্যয়ে যথেচ্ছ অনিয়ম অগ্রযাত্রার পথে বড় বাধা। সাথে নীতিনির্ধারকদের সদিচ্ছার অভাব তো আছেই।
চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের নির্বাহী পরিচালক এম জাকির হোসেন খান বলেন, নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যারা আছে এবং সরকারের যারা উচ্চমহলে গত ১৫-১৬ বছরে বা আগেও দেখেছি, তারা আমদানিনির্ভর বিদ্যুৎ সরবরাহকে সবসময় প্রমোট করে এবং জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর। কারণ ওখান থেকে তারা দুইটা বা তিনটা পর্যায়ে কমিশন পায়। নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে তারা একটা পর্যায়ে কমিশন পায়, সেটা হলো অনুমোদনের সময়।
অধ্যাপক এম শামসুল আলম বললেন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনকে (বিআরসি) যে ক্ষমতা দেয়া আছে, সেসব প্রক্রিয়ায় যদি প্রকল্প নেয়া হতো, প্রতিটা টাকার হিসাব বুঝে নেয়ার জন্য বিআরসিতে স্টেকহোল্ডার নিয়ে যদি তদারকি কমিটি থাকতো, মনিটরিং কমিটি থাকতো, তাহলে এ বিষয়গুলো যথাযথ হতো। অর্থাৎ মানুষের অংশগ্রহণ দরকার, মানুষের ক্ষমতায়ন দরকার।
দেশীয় অর্থের ওপর নির্ভর না করে বিদেশি বিনিয়োগ আনার ওপর জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। এম জাকির হোসেন খান বলেছেন, সরকার যদি নবায়নযোগ্য জ্বালানির হার ২০৪০ বা ৪১ সালে ৪০ শতাংশ করতে চায়, গড়ে প্রতি বছর প্রায় এক থেকে এক দশমিক ছয় বিলিয়ন ডলার লাগবে। এর জন্য টাকা অভ্যন্তরীণ ব্যাংকগুলো থেকে পাবে, অথবা সরকার নিজে বিনিয়োগ করবে অথবা বিদেশি বিনিয়োগ আসবে। এই তিনটা মিলে নবায়নযোগ্য জ্বালানির একটা ফাইন্যান্স রোডম্যাপ থাকা উচিত ছিল। স্ট্রাটেজি থাকা উচিত ছিল।
অর্জনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে সরল স্বীকারোক্তি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের (ইডকল)। প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক আলমগীর মোর্শেদ বলেন, বাংলাদেশের সোলার রুফটপের সূচনা হয় বাসা-বাড়িতে। সেটার কিছুটা ব্যর্থতা বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানির গতিতে বাধা হিসেবে কাজ করে। যে কোনোভাবে বাংলাদেশে এর প্রতি আস্থা নষ্ট হয়ে যায়, নির্দিষ্ট এই একটি প্রকল্প ব্যর্থ হওয়ায়।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশের উচিত এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে টেকসই শক্তির অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করা।


